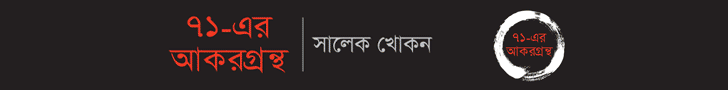‘বাহাপরব’ উৎসবের কথা অনেকেরই হয়তো অজানা। সাঁওতালদের অন্যতম প্রধান এ উৎসব খুব কাছ থেকে দেখেছি বহুবার। সাঁওতাল ভাষায় ‘বাহা’ মানে ‘ফুল বা কুমারীকন্যা’ আর ‘পরব’ মানে ‘অনুষ্ঠান’ বা ‘উৎসব’। অনেকেই এটিকে বসন্ত উৎসবও বলে থাকে। প্রতি চৈত্রের শেষে সাঁওতাল গ্রামগুলোয় চলে এ উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা। বসন্তে শাল, শিমুল, পলাশ, মহুয়া ও চম্পা ফুল ফোটে চারদিকে। বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয় প্রকৃতি। কিন্তু এ উৎসবের আগে সাঁওতাল নারীরা ফুল উপভোগ করা থেকে বিরত থাকেন।
শাল ফুলকে সাঁওতালরা বলে ‘সারজম বাহার’। শিকার থেকে শুরু করে নানা কারণে শালগাছ আদিবাসীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়টিতে সিদু-কানু জুলুম আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমবেত হতে গ্রামে গ্রামে পাতাসমেত ছোট শালের ডাল পাঠিয়েছিলেন। তাদের কাছে শালের ডাল একতার প্রতীক ও ঐতিহ্যের একটি অংশ। সময়ের হাওয়ায় এখন বদলে গেছে অনেক কিছু। সারা দেশে ক্রমেই শালবন ছোট হয়ে আসছে। তবু আদিবাসীদের সঙ্গে এ শালবনের বন্ধুত্ব কমেনি এতটুকু।
বাহাপরব উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম দিনাজপুরের মহেশপুর গ্রামে। এই গ্রামটিতে প্রায় ২০০ সাঁওতাল পরিবারের বাস। একদিকে চরম দারিদ্র্য আর অন্যদিকে ধর্মান্তরিত হওয়ার হাতছানি। কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও অধিকাংশই আদিবাসীই এখানে টিকিয়ে রেখেছে পূর্বপুরুষদের আচার, রীতিনীতি ও বিশ্বাসগুলোকে। মহেশপুর যখন পৌঁছি, তখন মধ্য দুপুর। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে নির্জন জায়গায় চলছে বাহাপরব উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা। গোত্রপ্রধান বা জগ মাঝি বাঠু সরেন। তার মুখেই শুনি সাঁওতালদের বাহাপরব উৎসবের আদ্যোপান্ত। আদিবাসী এ উৎসবটি তিন দিনের। তবে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানই প্রধান। উৎসবের মূল উদ্দেশ্যে জাহেরএরা, গোসায়এরা, মরেকু, তুরইকু নামক দেবতা বা বোঙ্গার সন্তুষ্টি লাভ। নিয়ম মেনে বাহাপরবের এক দিন আগে আদিবাসী গ্রামে ‘জাহের থান’ ও ‘মাঝি থান’ নানাভাবে সাজানো হয়। সাঁওতালরা মনে করে নতুন সবুজ পত্রপল্লবে সেজে ওঠা ধরণি হলো পবিত্র কুমারীকন্যার প্রতীক। তাই পরব শুরুর পূজায় দেবতাকে শাল ও মহুয়া ফুল উৎসর্গ করা হয়। অনুষ্ঠানে সাঁওতালরা শাল ফুলকে বরণ করে নেন নানা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে। মূলত এর পরই সাঁওতাল নারীরা খোঁপায় রং-বেরঙের ফুল পরেন।
মহেশপুর গ্রামের একটু উঁচু জায়গায় তিনটি ধনুক গেড়ে দেওয়া হয়। একটি কুলার মধ্যে রাখা হয় চাল, সিঁদুর, ধান, দুর্বা ঘাস আর বেশ কিছু শাল ফুল। পাশেই বলি দেওয়া হয়েছে কয়েকটি লাল মুরগি। এটিই বাহাপরবে পূজার নিয়ম। বলি দেওয়া মুরগি দিয়ে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন শুরু করে দু-একজন। বাহাপরব উৎসবকে ঘিরে বিকেলের দিকে আশপাশের সাঁওতালদের সম্মিলন ঘটে সেখানে। তাদের মাদলের তালে তালে চলে নানা আনন্দ আয়োজন। বাহাপরব উৎসবে সাঁওতাল গ্রামের এক প্রান্তে নির্দিষ্ট স্থানে তারা পূজার আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন। এ উপলক্ষে নির্দিষ্ট দিনে ‘জাহের থানে’ শালগাছের খুঁটি দিয়ে অন্যান্য বোঙ্গার জন্য প্রতীক হিসেবে ছোট ছোট কয়েকটি চালাঘর তৈরি করা হয়। সাধারণত গ্রামের সাঁওতাল যুবকরাই জঙ্গল থেকে শালগাছ কেটে আনেন এবং চালাঘর তৈরিকে সাহায্য করেন। পূজার জায়গাটি ভালোভাবে নিকানো হয় গোবর দিয়ে। চালের গুঁড়া দিয়ে আঁকা হয় চমৎকার সব আলপনা।
পূজায় পুরোহিত বা মহতকে উপোস থাকতে হয়। আগের রাত্রে রাত্রিযাপন করতে হয় মাটিতে শুয়ে। পূজার জন্য দেবতার আসনও প্রস্তুত করেন তিনি। উপকরণ হিসেবে ফল-মূল, চাল, সিঁদুর, ধান, দুর্বা ঘাস আর নানা সামগ্রী তিনি কুলোতে সাজিয়ে রাখেন। এ ছাড়া একটু উঁচু জায়গায় তিনটি ধনুক গেড়ে তাতে সিঁদুর মাখিয়ে দেওয়া হয়। তাদের কাছে তীর ও সিঁদুর বিপ্লবের প্রতীক।
বাহাপরব উৎসবে পুরোহিত বা মহতকে তার বাড়ি থেকে বন্দনা করে পূজাস্থলে নিয়ে আসেন সাঁওতালরা। এ সময় তিনি উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করেন। অতঃপর বলি দেওয়া হয় কয়েকটি লাল মুরগি বা পশু। এ সময় পুরোহিত গ্রামের কল্যাণের জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন। শেষে বলি দেওয়া পশুর মাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে সাঁওতাল গ্রামের সবাইকে খাওয়ানো হয়।
পূজা শেষে বিকেলের দিকে পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে সবাই দল বেঁধে গ্রামে ফিরে আসেন। এ সময় নারীরা তাকে ঘিরে সাঁওতালনৃত্য পরিবেশন করেন। পুরোহিতের মাথায় থাকে শাল ফুলের ডালা। তার সঙ্গে এক যুবক মাটির কলসিতে এক কলসি জল ভরে মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি এগোতে থাকে। এক-একটি বাড়ির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় গৃহস্থ নারীরা ওই পুরোহিত ও যুবকটির পা ধুইয়ে দেন। তারাও প্রত্যেক গৃহস্থ নারীকে ঝুড়ি থেকে পবিত্র শাল ফুল প্রদান করেন। তারা শাল ফুল গ্রহণ করে তাদের ভক্তি দেন। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে পূজাস্থল থেকেই সাঁওতাল গৃহস্থ নারীরা শাল ফুল গ্রহণ করেন পরম ভক্তির সঙ্গে। তাদের বিশ্বাস বাহাপরবে এভাবেই ফুলরূপে দেবতা বা বোঙ্গা তার ঘরে প্রবেশ করেন। শাল ফুল বিতরণ শেষে শুরু হয় আনন্দ নৃত্য। সাঁওতাল পুরুষরা বাজান মাদল-ঢোল। তালে তালে ঝুমুর নৃত্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নারীরা। খোঁপায় শালসহ নানা রঙের ফুল ঝুলিয়ে, হাত ধরাধরি করে নাচেন তারা। এভাবে বাহাপরব উৎসবের প্রথম দিনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানকে বলা হয় ‘বাহা বাস্কে’ (এক রাতের বাসি)। এদিন সাঁওতালরা একে অপরের গায়ে পানি ছিটানো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাদের বিশ্বাস পানি ছিটানোর মধ্য দিয়ে পুরনো যত হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা আছে তা দূর হয়ে যায়। ফলে পরস্পরের সঙ্গে তৈরি হয় বন্ধুত্বের সেতুবন্ধ। উৎসবের তৃতীয় দিনটিতে চলে শুধুই নানা আনন্দ আয়োজন। এ আনন্দ-উৎসবে গান ও নারী-পুরুষের সম্মিলিত বাহা দান ও জাতুর দান নাচ পরিবেশন করেন সাঁওতালরা।
একসময় ‘বাহাপরব’ উৎসবটি পালিত হতো ধুমধামের সঙ্গে। কয়েক গ্রামের সাঁওতালরা তখন এক হয়ে নানা আচার ও আনন্দ নৃত্য পরিবেশন করতেন। দারিদ্র্য, অবহেলা, ভূমিকেন্দ্রিক দখল আর নির্যাতনের ফলে সাঁওতালদের বাহাপরব উৎসবও আজ পালিত হচ্ছে ঢিমেতালে। আবার ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা বাহাপরব পালন করলেও সেখানে আদি রীতিটি প্রায় অনুপস্থিত। ধর্মকেন্দ্রিক আচারগুলো তারা পালন করে না। পূর্বপুরুষদের আদি রীতিগুলো ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের কাছে আজ কুসংস্কার মাত্র। ফলে একই গ্রামে এখন সাঁওতালরা বাহাপরব উৎসব আয়োজন করছেন আলাদাভাবে। আদি ধর্মমতের সাঁওতালরা আদিরীতি মেনে আর ধর্মান্তরিত আদিবাসীরা শুধু নাচ-গানের মাধ্যমেই বাহাপরবের উৎসব শেষ করেন। ফলে এ আদি উৎসবের আদি রূপটি আজ প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে।
এ দেশে বসবাসরত আদিবাসীদের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত নিজস্ব আচার, উৎসব ও সংস্কৃতি। দারিদ্র্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠের আগ্রাসী সংস্কৃতির চাপে আজ তা প্রায় বিপন্ন। তবু আদিবাসীরা ধরে রেখেছেন নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। তাই বাহাপরবের মতো উৎসবগুলো টিকিয়ে রাখতে সরকারিভাবেও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। স্বাধীন এ দেশে সব জাতির উৎসবই পালিত হোক। সাঁওতালদের বাহাপরব হোক আনন্দের। উৎসবের আনন্দ-উল্লাস আর বিশ্বাসের জোয়ারে ভেসে যাক তাদের চিরচেনা দুঃখগুলো।
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক দেশ রূপান্তরে, প্রকাশকাল: ৩১ মার্চ ২০১৯
© 2019, https:.