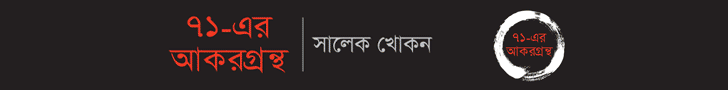পার্বত্য অঞ্চলে পানির কষ্ট শুরু হয় সাধারণত শীতকাল থেকে, যা বর্ষার আগ পর্যন্ত চলে। পাহাড়ে জনবসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পানির সংকটও বাড়ছে। এই সংকট দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়, যেখানে আদিবাসীদের বসবাস, সেখানে আরও প্রকট। গণমাধ্যমে প্রকাশিত জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিবেদন বলছে, রাঙ্গামাটি জেলার ৪০ শতাংশ, বান্দরবানে ৫৩ শতাংশ আর খাগড়াছড়ি জেলার ৫৬ শতাংশ মানুষের জন্য তারা পানির ব্যবস্থা করতে পেরেছে। বসবাসকারী বাকিরা পানির জন্য নির্ভর করে প্রাকৃতিক উৎসের ওপর।
ঢাকা ওয়াসার পানি শতভাগ সুপেয় কি না তা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। কোন কোন এলাকায় পানি থাকে না, কোন এলাকার পানি পানের অনুপযোগী, তা উঠে আসছে গণমাধ্যমের সংবাদে। কিন্তু দেশের তিন পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম পাহাড়ে পানির তীব্র সংকটের সংবাদ গণমাধ্যমে আমরা খুব কমই পেয়ে থাকি।
খাগড়াছড়ির সাজেকে বেড়ানোর স্মৃতি বহুদিন আমাদের আন্দোলিত করে। কিন্তু শুকনো মৌসুমে সাজেকের কংলাকের দুর্গম পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী নারীদের পানি সংগ্রহের কষ্টের কথাগুলো আমাদের কান অবধি এসে পৌঁছায় না। সেখানে এখন প্রায় ৮০০ ফুট নিচে পাহাড়ের খাদ থেকে এবং দুই কিলোমিটার দূরের পাহাড়ি ঝিরি থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করছেন আদিবাসী নারীরা।
পার্বত্য অঞ্চলে পানির কষ্ট শুরু হয় সাধারণত শীতকাল থেকে, যা বর্ষার আগ পর্যন্ত চলে। পাহাড়ে জনবসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পানির সংকটও বাড়ছে। এই সংকট দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়, যেখানে আদিবাসীদের বসবাস, সেখানে আরও প্রকট। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সেখানে সরকার আসলে কী করছে? গণমাধ্যমে প্রকাশিত জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিবেদন বলছে, রাঙ্গামাটি জেলার ৪০ শতাংশ, বান্দরবানে ৫৩ শতাংশ আর খাগড়াছড়ি জেলার ৫৬ শতাংশ মানুষের জন্য তারা পানির ব্যবস্থা করতে পেরেছে। বসবাসকারী বাকিরা পানির জন্য নির্ভর করে প্রাকৃতিক উৎসের ওপর। এসব অঞ্চলে গভীর নলকূপ ও চাপকলের সংখ্যা যথাক্রমে রাঙ্গামাটিতে ১ হাজার ৮৯৭টি, খাগড়াছড়িতে ৯ হাজার ৬৮৩টি আর বান্দরবানে ৭ হাজার ১০৮টি।
কিন্তু বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। সরকারিভাবে যে নলকূপগুলো ওই অঞ্চলে বসানো হয়েছে, সেগুলোর অর্ধেকেই পানি উঠে না। এসব অঞ্চলের বেশির ভাগ বিদ্যালয়েও নেই পানির ব্যবস্থা। পাহাড়ের ঝিরিগুলোতে শুকনো মৌসুমে পানি শুকিয়ে যায়। তলানিতে যেটুকু থাকে তাও হয় ময়লাযুক্ত। সে পানিই ছেঁকে ব্যবহার করতে হয় আদিবাসীদের। পানি ফুটিয়ে পান করারও উপায় নেই। ফলে শুকনো মৌসুমে ডায়রিয়াসহ পেটের পীড়ায় ভোগেন এখানকার মানুষ। অনেক জায়গায় কুয়োর ব্যবস্থা থাকলেও বর্ষায় ময়লাতে ভরে যায় কুয়োগুলো। তখন বৃষ্টির পানিই এখানকার মানুষদের একমাত্র ভরসা। মূলত পানির জন্য এক ধরনের সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হচ্ছে পাহাড়ের আদিবাসীদের।
রাঙ্গামাটিতে পানির জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি। জেলার দশটি উপজেলার মধ্যে কাপ্তাই, বাঘাইছড়ি, রাজস্থলী ও কাউখালীতে সংকট বেশি। শুকনো মৌসুমে এখানকার মেয়েরা কয়েক কিলোমিটার চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পানি সংগ্রহ করেন। বান্দরবান জেলার দুর্গমতম রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি ও আলীকদমে পানির সংকট সবচেয়ে বেশি। এ জেলার প্রায় চার লাখ মানুষের অর্ধেকের বেশি সরকারি-বেসরকারি পানি সরবরাহের আওতার বাইরে। বান্দরবানে সরকারিভাবে সাত হাজারের মতো নলকূপ, গভীর নলকূপ কিংবা পাতকুয়া স্থাপন করা হয়েছে। যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি অকেজো। এখানকার রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি ও আলীকদমের ৮০ শতাংশ মানুষ ঝিরি, খাল ও নদীর পানির ওপর নির্ভরশীল।

খাগড়াছড়ি জেলায় ছয় লাখেরও বেশি মানুষের বাস। প্রায় অর্ধেক মানুষই প্রাকৃতিক উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করেন। ফলে শুকনো মৌসুমে এ অঞ্চলে তীব্র পানির সংকট দেখা দেয়। বম ও খুমি আদিবাসী অধিকাংশই বসবাস করেন পাহাড়ের চূড়ায়। তাই পানি সংগ্রহের কষ্টটা তাদেরই বেশি। পানি সংগ্রহের কাজটি করেন মূলত আদিবাসী নারীরা। এ সময় প্রায় এক হাজার ফুট পাহাড়ের খাদে নেমে পানি সংগ্রহ করে তা চূড়ায় তুলে আনতে হয় তাদের।
এ ছাড়া পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষগুলোও সাধারণত ছড়া, ঝিরির ওপর নির্ভরশীল। ছড়াতে কূপ খনন করে কিংবা পাহাড় থেকে চুয়ে পড়া পানির মুখে বাঁশ বসিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করেন আদিবাসীরা। যা দিয়ে খাওয়া, রান্নাবান্নাসহ সংসারের দৈনদিন কাজ চলে। এই গ্রীষ্মে পানির উৎসগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় তারা পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে। খাওয়াসহ সংসারের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য পানি পাচ্ছেন না। সারা দিন জুমচাষে ব্যস্ত থাকা জুমিয়ারা এখন দিনের অর্ধেক সময়ই ব্যয় করছেন পানি সংগ্রহে।
পাহাড়ের আদিবাসীরা বলছেন, পানির উৎস থেকে পাথর তুলে নেওয়ায় এবং পাহাড়ে বন উজাড় হওয়ায় পাহাড়ি ঝিরিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার পাহাড়ধস এবং জনবসতি বাড়ার কারণে অনেক পানির উৎস ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক ঝরনা শুকিয়ে গেছে। ফলে পানির সংকট দিনে দিনে বাড়ছে। পাহাড়ে ঝিরি ও ছড়াগুলো বাঁচাতে না পারলে পানির এই কষ্ট আরও বাড়বে।
পার্বত্য অঞ্চলের পানি সংকটের কারণ তুলে ধরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টি কম হওয়া, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, আর বন-পাহাড়ে লাগানো কিছু গাছপালা অনেক পানি টেনে নিচ্ছে। ফলে শুকনো মৌসুমে পাহাড়ে পানি সংকট তীব্রতর হচ্ছে। আবার জীববৈচিত্র্য ও পাহাড়ের বন ধ্বংস হওয়ার কারণেও তিন পার্বত্য জেলার ছড়া ও ঝরনা শুকিয়ে যাচ্ছে। বনায়ন করে ছড়া ও ঝরনায় পানির ধারা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা, কাপ্তাই হ্রদের পানি পাইপের মাধ্যমে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া, বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য পার্বত্যবাসীর মধ্যে অধিক পরিমাণে ট্যাংক সরবরাহ করার উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তারা। এতে পানির সংকট অনেকাংশেই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। তবে তারা বলছেন, পার্বত্য অঞ্চলের পানি সংকট নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া প্রয়োজন। আর সেটি করতে হবে সরকারকেই।
নিরাপদ পানির বিষয়টি মানবাধিকারের অংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে জাতিসংঘের পানিবিষয়ক ২০১১ সালের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে। এ ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপদ পানির অধিকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের ২০১৩ সালের পানি আইনে। সেখানে ২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছেÑ ‘সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়োনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানির অধিকার সর্বাধিকার হিসেবে বিবেচিত হইবে।’ এ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) ১৭টির মধ্যে ৬ নম্বর লক্ষ্যমাত্রায় নিরাপদ পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এসব কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা বিধানে বাংলাদেশকে দিশারি রাষ্ট্র হিসেবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পানি নিরাপদ না হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। আর স্বাস্থ্য ভালো না হলে সরকারের উন্নয়নও টেকসই হবে না। নিরাপদ পানির উৎস ও সরবরাহ কার্যক্রমকে এখনই ঢেলে সাজাতে হবে।
শুধু রাজধানীর নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহই নয়, পার্বত্য অঞ্চলগুলোতেও পানির সংকট নিরসনে নতুন করে কর্মপরিকল্পনা করা প্রয়োজন। নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শেখ হাসিনা সরকার। পানি নিয়ে পাহাড়িদের কষ্টের কথাগুলোও সরকার গুরুত্বের সঙ্গে দেখবে বলে আশা রাখি। পার্বত্যবাসীর নিরাপদ পানি সরবরাহের দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে হাতে নিতে হবে কার্যকর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। এর মধ্য দিয়ে পাহাড়ে আদিবাসীদের পানির কষ্ট দূর হবে-আমরা এমনটাই প্রত্যাশা করি।
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক দেশ রূপান্তরে, প্রকাশকাল: ১২ মে ২০১৯
© 2019, https:.