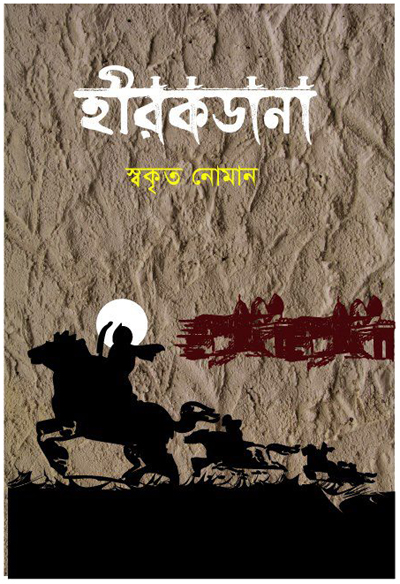সমন্বিত আক্রমণ ছিল অপারেশন জ্যাকপট

১৯ এপ্রিল, ১৯৭১। আমরা তখন ভারতের টাকিতে, ত্বকীপুর ইয়ুথ ক্যাম্পে। মেজর জলিল তখনও যাননি। ক্যাম্পের দায়িত্বে ক্যাপ্টেন শাহজাহান আলী। ওখানে শুধু পিটি-প্যারড করানো হত। ট্রেনিংয়ের দেরি দেখে আমরা উদগ্রীব। বাল্যবন্ধু সন্তোষ কুমার বিশ্বাস তখন পড়ত টাকি কলেজে। ওই কলেজের এক শিক্ষক ছিলেন সিপিএম নেতা। নাম বিমল চন্দ্র রায়। যুদ্ধে যাওয়ার আগ্রহের কথা শুনে তাঁর মাধ্যমেই সন্তোষ আমাদের নিয়ে যায় কলকাতায়।
আমজাদুল হোসেন, আবদুল হাই, মোজাইদুল হোসেন, লুৎফর রহমান, আবদুল ওয়াহিদ, শাহদাত হোসেনসহ আমরা সাতজন কথা বলি সিপিএম প্রধান বিমান বোসের সঙ্গে। তিনিই নিয়ে গেলেন জ্যোতি বসুর বাড়িতে। জ্যোতি বসু বললেন: ‘‘ভিয়েতনাম বা পৃথিবীর অন্য দেশের মতোই এ যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে। তাই তোমাদেরও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। তোমরা এখানে থেকে যুদ্ধটা আসলে কী, তা বুঝে নাও।’’
বিমান বোসের অধীনে নারকেলডাঙ্গা কলেজে আমরা সাত দিন ট্রেনিং নিই। আমাদের বোঝানো হচ্ছিল নানা কথা: ‘‘তোমরা খালি হাতেই সশস্ত্র সংগ্রাম করবে। কোনো অস্ত্র লাগবে না। বরং তোমরাই অস্ত্র সংগ্রহ করবে।’’
ট্রেনিং শেষে বোঝা গেল আসল উদ্দেশ্যটা। এক ব্যক্তি এসে বললেন: ‘‘বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। সেটা যত বছরই লাগুক। দেশ স্বাধীন হলে তোমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে। যারা দেশ স্বাধীন করবে অস্ত্রগুলো তখন তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে। মনে রাখবে, ক্ষমতাই হল মূল উৎস। আওয়ামী লীগ দেশ স্বাধীন করবে, আর তোমরা আওয়ামী লীগের কাছ থেকেই ক্ষমতা নিয়ে নিবে।’’
কথাগুলো আমাদের ভালো ঠেকল না। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের স্বাধীনতার জন্য ঘর ছেড়েছি। তাই নীতিগতভাবে কথাগুলো মেনে নিতে পারলাম না। প্রতিবাদ করেই সবাই পুনরায় ফিরে গেলাম ইয়ুথ ক্যাম্পে।
ভারী চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে কথা বলছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডো মোহাম্মদ খলিলুর রহমান। পাশ থেকে আমরা শুধু বলি: ‘‘তারপর?’’
তিনি মুচকি হাসেন। অতঃপর আবার বলতে শুরু করেন:

৮ জন বাঙালি সাবমেরিনার ফ্রান্স থেকে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে চলে আসেন ভারতে। ভারতীয় নৌবাহিনীর সহযোগিতায় তারা সমন্বিত দল গঠন করার উদ্যোগ নেন। ১২ মে, ১৯৭১। ক্যাম্পে তখন পাঁচ হাজারের মতো যুবক। সবাইকে ফলিং করিয়ে তার মধ্য থেকে তাঁরা ১২০ জনকে সিলেক্ট করেন। শারীরিক গঠন আর সাঁতার জানাটাই ছিল মাপকাঠি। বাড়ির একমাত্র ছেলে হলেই আনফিট করে দেওয়া হত। নদীর পাড়ের ছেলেরা টিকে যায় সবচেয়ে বেশি। সে হিসেবেই আমাকেও তাঁরা নিয়ে নিলেন।
টাকি থেকে প্রথমে কল্যাণী এবং পরে ট্রাকে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় পলাশীতে। সেখানে ভাগিরথী নদীর তীরে জঙ্গল পরিষ্কার করে আমরা ক্যাম্প করি। এরপরই শুরু হয় ট্রেনিং। প্রথমেই শপথ নিই, ‘দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেই আমি স্বেচ্ছায়, স্ব-প্রণোদিতভাবে এই আত্মঘাতী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছি।’
ট্রেনিংয়ে ভারতীয় নৌবাহিনী আমাদের শেখায় বিশেষ ধরনের সাঁতার। পানির নিচে শরীর, ওপরে শুধু নাক ও চোখ রেখে সাঁতার দিতে হত। এ পদ্ধতিতে সাঁতার কেটে নিঃশব্দে যে কোনো মানুষের পাশ দিয়েই চলে যাওয়া যেত। সবচেয়ে কঠিন ছিল মাইন অ্যাসেম্বল এবং পানির নিচ দিয়ে সেটা নিয়ে গিয়ে জাহাজে সেট করা। নৌবাহিনীর ৩ বছরের ট্রেনিং আমরা নিই ৩ মাসে। আমার নৌ কমান্ডো নম্বর ছিল ০০৬০। ট্রেনিং চলাকালে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান নন্দা, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও কর্নেল এম এ জি ওসমানী সাহেব এসেছিলেন।
এই প্রশিক্ষণ শেষেই কি অপারেশনে অংশ নেন?
কম্যান্ডো খলিলুর রহমানের উত্তর:
হ্যাঁ, প্রশিক্ষণ শেষেই পরিকল্পনা হয় চট্রগ্রাম, মংলা সমুদ্র বন্দর, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে একই দিনে একই সময়ে বিষ্ফোরণ ঘটানোর। সমন্বিত এই আক্রমণের নাম দেওয়া হয় ‘অপারেশন জ্যাকপট’।
অপারেশন জ্যাকপটের আদ্যোপান্ত শুনি মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের জবানিতে। তাঁর ভাষায়:
আমরা প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ছিলাম ১৬০ জন। চট্রগ্রামের জন্য ৬০ জন, মংলার জন্য ৬০ জন, চাঁদপুরের জন্য ২০ জন ও নারায়ণগঞ্জের জন্য ২০ জন করে ৪টি গ্রুপ গঠন করা হল। আমি ছিলাম মংলা বন্দরের গ্রুপে। কমান্ডার ছিলেন প্রয়াত আহসান উল্লাহ বীর প্রতীক।
৭ আগস্ট, ১৯৭১। ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে আমাদের নেওয়া হয় বেরাকপুর ক্যাম্পে। সেখানে গঙ্গা নদীতে নামিয়ে একটি জাহাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেওয়া হয়। পরে ক্যানিং থেকে দেশি নৌকায় রায়মঙ্গল নদী পার হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা সুন্দরবনের ভেতর কৈখালি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে এসে পৌঁছি। ওখানে ছিলেন ক্যাম্প কমান্ডার জর্জ মার্টিস, লেফটেন্যান্ট কফিল। মূলত প্র্যাকটিসের জন্যই স্থলপথে না এনে ভয়াল নদীপথে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়।
অতঃপর সমুদ্রের পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে সুন্দরবনের ভেতর প্রথমে উঠি কালাবগি নামক এক গ্রামে। পরে ক্যাম্প গড়ি সুতারখালিতে। ২০ জন করে আমরা তিনটি দলে ভাগ হই। তিনটি দলের উপ দলনেতা মজিবর রহমান, আফতাব উদ্দিন ও আমি। আমাদের সাপোর্ট করতে আসে ২০ গেরিলা। তাদের কমান্ডার ছিলেন খিজির আলী বীর বিক্রম। অতঃপর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকি আমরা।
আগেই বলা ছিল ৪ বন্দরে আক্রমণের জন্য সব ক’টি গ্রুপকে একসঙ্গে নির্দেশ প্রদান করা হবে। এ জন্য প্রত্যেক গ্রুপকে দেওয়া হয় একটি করে রেডিও। বলা হল– তোমরা ১৩ আগস্ট থেকে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে আকাশবাণী ‘খ’ কেন্দ্র শুনবে। যে কোনো দিন পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে তোমাদের একটা গান শোনানো হবে। গানটি হল, ‘আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান…।’ এই গান শুনলেই বুঝতে হবে প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এর ২৪ ঘণ্টা বা তারও পরে শোনানো হবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটি গান। গানটি হল, ‘আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি…।’ এই গানটি শুনলে ওইদিনই টার্গেটে হিট করতে হবে।
১৩ আগস্ট রেডিওতে আমরা প্রথম গানটি শুনলাম। কিন্তু দ্বিতীয় গানটি শোনানো হল ৪৮ ঘণ্টা পর, অর্থাৎ ১৫ আগস্ট সকালে। আহসান উল্লাহ সাহেব সবাইকে ডেকে নির্দেশ দিলেন হিট করার। আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম। সাঁতার কাটার জন্য পায়ে শুধু ফিন্স ও একটা সুইমিং কসটিউম পরা। গামছা দিয়ে শরীরে পেঁচিয়ে নিলাম মাইনটি। জাহাজের গায়ে মাইন লাগানোর জন্য সঙ্গে ছিল একটা ডেগার।
গেরিলারা রেইকি করে এল দিনের বেলায়। ওইদিন সন্ধ্যার পরই আমাদের শপথ করানো হল এ মর্মে: ‘আমরা সবাই ভাই ভাই। দেশের জন্য জীবন দিতেও দ্বিধা করব না। আরেক জনকে বিপদে ফেলব না এবং বিপদ দেখে সরে পড়ব না।’ রাতে নৌকায় করে রওনা হলাম। স্রোত ছিল প্রতিকূলে। ফলে ভোরের দিকে পৌঁছালাম মংলা বন্দরের অপর তীরে, বানিয়াশান্তা গ্রামে। আমরা অবস্থান নিই বেড়িবাঁধের নিচে।
অপারেশন জ্যাকপট’ ও পাকিস্তানি সেনাদের টর্চারের বর্ণনা দিচ্ছেন নৌ কমান্ডো খলিলুর রহমান:
গকথা ছিল মধ্য রাতে অপারেশন করার। কিন্তু তা হল না। তখন সূর্য উঠছে। শরীরে সরিষার তেল মেখে কসিটউম পরে নিই। বুকে মাইন বেঁধে পানিতে নেমে প্রকাশ্য দিবালোকেই আমরা অপারেশন করি। বন্দরের জাহাজগুলোতে মাইন লাগিয়ে যে যার মতো দ্রুত সরে পড়ি। পানির উপরে তখন পাকিস্তানিদের গানবোট। সকাল তখন ৯টার মতো। একে একে বিষ্ফোরিত হতে থাকে মাইনগুলো। এটাই ছিল ‘অপারেশন জ্যাকপট’। সব মিলিয়ে এই অপারেশনে ৪টি বন্দরের মোট ২৬টি জাহাজ আমরা ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।
মুক্তিযোদ্ধা নৌ কমান্ডো মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের মুখে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও ত্যাগের কথা শোনার ফাঁকে একটু পেছনে ফিরে যাই, শুনি তাঁর শৈশব-কৈশোরের গল্প।
পিতা আয়জুদ্দিন বিশ্বাস ও মা ওয়ালিউর নেছার সপ্তম সন্তান তিনি। গ্রামের বাড়ি সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার ভাতশালা গ্রামে। বাবা ছিলেন ভূস্বামী। অগাধ জমিজমার মালিক। তাঁর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি ভাতশালা প্রাইমারি স্কুলে। ১৯৬৬ সালে এসএসসি পাশ করেন টাউন শ্রীপুর এসসি (শরৎচন্দ্র) হাই স্কুল থেকে। অতঃপর বাগেরহাট কলেজে স্নাতক সম্মানে ভর্তি হন। ১৯৭৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এমএসসি করেন তিনি। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন খলিলুর রহমান।
সে সময় দেশের খবরগুলো কীভাবে পেতেন ওঁরা, সে কথা জানতে চাই আমরা। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জানালেন:
‘‘আমরা খবর পেতাম না, খবর তৈরি করতাম। বিএল কলেজ আর আজম খান কমার্স কলেজ ছিল খুলনা শহরেই। অনেক প্রগতিশীল ছাত্রনেতা ছিলেন সেখানে। তাদের সঙ্গে আমার সখ্যতা ছিল। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়ন করি। অ্যাডভোকেট আবদুল জব্বার সাহেব ছিলেন নেতা। পরে বাগেরহাট কলেজে ভর্তি হয়ে ছাত্রলীগে যোগ দিই। কলেজ শাখার সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ছিলাম আমি।’’
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ এই বীর মুক্তিযোদ্ধা শোনেন রেডিওতে। তাঁর ভাষায়:
‘‘আমার চাচা আবদুল জব্বার বিশ্বাস থাকতেন খুলনা শহরেই। তাঁর বাসায় থেকেই আমি আর বড় ভাই এরশাদ আলী লেখাপড়ি করি। সবাই মিলে রেডিওতে শুনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি। তিনি বললেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।’ ভাষণের পর সবার মনে যেন আগুন লাগল। স্পষ্ট হল, সংগ্রাম ছাড়া পথ নেই। ভাষণেই সব নির্দেশনা দেওয়া ছিল। ভাষণের মধ্যেই নিহিত আছে গোটা বাংলাদেশ। এর পরই খুলনায় কামরুজ্জামান টুকু, হিরন ভাই, আবদুল জামাল, ওয়াদুদ, বাচ্চু প্রমুখ মিলে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। খুলনা হয়ে ওঠে আন্দোলনের দুর্গ।’’
২৫ মার্চ, ১৯৭১এ ঢাকায় আর্মি নামে, এ খবর শোনার পর আপনারা কী করলেন?
‘‘২৫ মার্চের আগেই খুলনা শহর থেকে সাতক্ষীরায় চলে আসি। ক্যাপ্টেন শাহজাহান আলী ছিলেন গ্রামের লোক, আমার শিক্ষক। ২৯ মার্চের কথা। তাঁর নেতৃত্বে আশপাশের বিওপির কিছু বাঙালি ইপিআর, পুলিশের সদস্য নিয়ে দেবহাটা থানার সামনে চলল প্রশিক্ষণ। আমিসহ আমজাদুর হোসেন, লুৎফর রহমান, আবদুল জলিল বিশ্বাস, মুজাহিদ হোসেন, আবদুল হাই, আবদুল ওয়াহিদ, শাহদাত হোসেন তাতে অংশ নিই। থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছিল ১৪টার মতো। ১৮ এপ্রিল যশোর থেকে পাকিস্তানি সেনারা সাতক্ষীরা দখল করে এবং কালিগঞ্জ পর্যন্ত চলে আসে। তখনও সবার ট্রেনিং শেষ হয়নি। সাতক্ষীরা শহরের অদূরে পারুলিয়া ব্রিজ ও সাপমারা নদীর কাছে আমরা প্রথম একটা প্রতিরোধ গড়ি। কিন্তু পেরে উঠি না। তবুও লক্ষ্য ছিল আমরা আছি এই সিগনালটা দেওয়া। তাদের আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আমরা টাউন শ্রীপুর দিয়ে ইছামতি নদী পার হয়ে ভারতের টাকিতে গিয়ে উঠি।’’
‘অপারেশন জ্যাকপট’এর পর আপনারা কি আপনাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন?
প্রশ্ন শুনে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডো খলিলুর খানিকটা নিরব থাকেন। অতঃপর চোখের কোণে জমে কয়েক ফোঁটা জল। আমরা তখন নিরব থাকি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলেন:
‘‘১৮ আগস্ট, ১৯৭১। ‘অপারেশন জ্যাকপট’ শেষে ফেরার পথে সাতক্ষীরার বুদহাটাতে আমরা সাতজন পাকিস্তানি সেনাদের অ্যাম্বুসের মুখে পড়ি। নদীপথে আমরা নৌকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সবাই প্রচণ্ড ক্লান্ত। একজন পাহারা দিলে বাকিরা ঘুমাত। রাত তখন ১টা। পাহারার দায়িত্ব ছিল মোহসিনের। হঠাৎ চারদিকে গুলির শব্দ। নৌকার ওপর লাইট মেরে পাকিস্তানি সেনারা গুলি ছুঁড়ছে। আমাদের না জাগিয়েই মোহসিন নিজের প্রাণ বাঁচাতে সাঁতরিয়ে পালিয়ে গেল। চোখ খুলে দেখি চারপাশ থেকে শুধু গুলি আসছে। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে এসএমজি আর দুইটা করে ম্যাগাজিন। যা দিয়ে মাত্র ২৫ গজ দূরে আঘাত করা যায়। আমরা পেরে উঠলাম না। ওখানেই আফতাব উদ্দিন ও সাতক্ষীরার কাটিয়া গ্রামের সিরাজুল ইসলাম মারা যায়। ডাঙায় ওঠার আগেই আমরা অস্ত্র ফেলে দিই। বন্দি হই মুজিবর রহমান, ইমাম বারি, ইমদাদুল হক ও আমি। ওরা বুঝে গেল আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আমরা তা স্বীকারও করলাম। কিন্তু নৌ কমান্ডোর পরিচয় এড়িয়ে গেলাম।’’
পাকিস্তানি সেনাদের টর্চারের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। অতঃপর বলতে থাকেন:
‘‘ওরা তো মানুষ ছিল না। চোখ বেঁধে, সারা শরীরে রড দিয়ে পিটিয়ে এক পর্যায়ে আমার দুই হাতের ওপর দুইজন দাঁড়িয়ে পড়ে। আরেক জন রড দিয়ে আমার পায়ের তলায় পেটাতে থাকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমার কোমর পর্যন্ত অবশ হয়ে যায়। মারের আঘাতে আমার মুখের সামনের সারির দাঁত ভেঙে যায়। এখানেই শেষ নয়, একদিন ইটের খোয়ার রাস্তায় জিপ গাড়ির সঙ্গে আমার পা বেঁধে টেনে নিয়ে গেল। পেটের চামড়া উঠে গিয়ে রক্ত পড়ছিল তখন। আমি ‘মা গো’, ‘বাবা গো’ বলে চিৎকার করছিলাম। উত্তেজিত হয়ে তারা বেয়নেট দিয়ে আমার শরীরে খোঁচায়। বাম হাতের কব্জিতে এখনও সে দাগ আছে। একবার সাতক্ষীরা থেকে আসে এক ক্যাপ্টেন। সঙ্গে রাজাকার কমান্ডার আবদুল্লাহ হিল বাকী। তার ছোট ভাই গালিব বর্তমানে জামাত নেতা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।’’
‘‘পরে আমাদের নিয়ে আসা হয় সাতক্ষীরায়, ডায়মন্ড হোটেলে। সেটি ছিল পাকিস্তানিদের টর্চার সেল। মেঝেতে যারা পড়েছিল, সবার শরীর রক্তমাখা। প্রতি রাতে মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনতাম। ৭ দিন চলল টর্চার। ডাকবাংলোর সামনে কবর খুঁড়ে সেখানে নিয়ে বলেছে, ‘মুখ খুল, না হলে এখনই মেরে ফেলব’।
সেখান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় যশোর ক্যান্টনমেন্টে। সেখানে বাঁশের সঙ্গে ঝুলছিলেন অসংখ্য মানুষ। মেয়েরা উলঙ্গ অবস্থায়। কয়েক জনের স্তন কেটে নেওয়া হয়েছে। আমাদের বস্তায় ঢুকিয়ে গরম পিচের রাস্তায় সারাদিন ফেলে রাখা হত। নিয়মিত বসানো হত ইলেকট্রিক চেয়ারে। ইলেকট্রিক শকের কারণে সারা শরীর কাঁপত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। তারা বেয়নেট দিয়ে আমার মলদ্বার খুঁচিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।’’
‘‘এই সব নির্যাতনের কারণে আজও শরীরটা স্বাভাবিক হয়নি। মাঝে মাঝেই ঘুমের মধ্যে সে সব স্মৃতি এসে হানা দেয়। তখন ঘুমোতে পারি না। ১৯ সেপ্টেম্বর আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে যাই। সে সময়টার কথা ভাবলেই মনের মধ্যে ঘৃণা চলে আসে সহযোদ্ধা মোহসিনের প্রতি।’’
এরপরও যুদ্ধ করেছিলেন এই অসমসাহসী যোদ্ধা। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে মনিরামপুর হয়ে বনগাঁ টালিখোলা ক্যাম্পে উপস্থিত হয়েছিলেন ওঁরা। ওখানে ছিলেন ক্যাপ্টেন নাজমুল। ২২ সেপ্টেম্বরে তাঁদের পাঠানো ৯ নং সেক্টরের টাকিতে, ক্যাপ্টেন শাহজাহানের কাছে। পরে তাঁর অধীনেই স্থলযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন খলিলুর রহমান– ভাতশালা, দেবহাটা থানার যুদ্ধ এবং কুলিয়া ব্রিজ অপারেশনে।
এরপর দেশ স্বাধীন হল। ১৬ ডিসেম্বর খুলনা শহর বিজয়ের অভিযানে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা খলিলুর রহমান। ১৭ ডিসেম্বর খুলনা দখলমুক্ত করেন তাঁরা। সেদিন সাধারণ মানুষ তাঁদের গায়ে ফুল ছিটাতে থাকে। দেশ স্বাধীন হলেও তিনি হারান বড় ভাই এরশাদ আলীকে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে গেছেন, সে অপরাধে তাঁর চাচার বাসা থেকে বড় ভাইকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি আর্মি। তাঁর লাশটাও ফিরিয়ে দেয়নি।’’
স্বাধীনতার পরের পেক্ষাপটের কথা বলতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা খলিলুর রহমান বলেন:
‘‘যে যুবক মুক্তিযুদ্ধে তার শ্রেষ্ঠ সময়টা উৎসর্গ করল, তার শিক্ষা, অগ্রগতি, উচ্চাশা সব কিছুই বিসর্জন দিল, তাদের খালি হাতে বলা হল যার যার পেশায় ফিরে যেতে। এটা ছিল বড় একটা ভুল সিদ্ধান্ত। মুক্তিযোদ্ধারা নিরস্ত্র হয়ে গ্রামে ফিরল। অথচ তাদের শত্রু রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের হাতে তখনও অস্ত্র ছিল।’’
কথা উঠে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রসঙ্গে। তিনি বলেন:

‘‘মিলিশিয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা নেওয়ার সময় তালিকা করা হয়েছিল। সে তালিকা এক করলেই হত। এটা তো গোলাপ গাছ না যে একটা ঝরছে আরেকটা গজাচ্ছে। তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কমার কথা। সংখ্যা তো দিনে দিনে বাড়ে। দুই চারজন মুক্তিযোদ্ধা এটাকে ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। আর এর জন্য বেশি দায়ী কল্যাণ ট্রাস্টের অসাধু কর্মকর্তারা। তবে এখন সরকার প্রশংসনীয় উদ্যোগগুলোই হাতে নিয়েছে।’’
আহত হয়েও ঢাকার বাইরে বসবাস করায় সরকারের যুদ্ধাহতের তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করার আবেদন করতে পারেননি খলিলুর।। ফলে ভাতাও পান না। এ রকম অনেক ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা আছেন যাঁরা অভিমানে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন। তাদের খুঁজে বের করে তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করার কথা বললেন খলিলুর।
রাজাকারদের তালিকা প্রসঙ্গে নিজের মতামত অকপটে তুলে ধরেন তিনি:
‘‘এদের বিচার করার জন্য বঙ্গবন্ধু দালাল আইন গঠন করেছিলেন। সে সময় বিভিন্ন মেয়াদে কয়েক জনের সাজাও হয়েছিল। সে সময়টাতে রাজাকারদের তালিকা করা দরকার ছিল। এখন রাজাকারদের যে তালিকা আমরা পাই তা কিন্তু সে সময়ে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা। গ্রেফতার হয়নি এমন রাজাকাররা এখনও রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।’’
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় একে একে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। রাজাকার কামরুজ্জামানের ফাঁসির রায় অচিরেই কার্যকর হবে। বিচার নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অনুভূতি জানতে চাই আমরা। উত্তরে তিনি বলেন:
‘‘আমার দেশের পতাকা উড়েছে রাজাকারের গাড়িতে। তখন মনে হয়েছে আমি মাটিতে মিশে যাই। দেরিতে হলেও এদের বিচার হচ্ছে। স্বাধীন দেশের আদালতেই এদের দাঁড়াতে হচ্ছে, এটা ভাবলে ভালো লাগে। তবে এদের শাস্তির পাশাপাশি অবশ্যই উচিত জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা। স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাবিরোধীরা তো রাজনীতি করতে পারে না!’
যে দেশের স্বপ্ন দেখে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন, তা কি পেয়েছেন?
‘‘সময়ের প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছি। দেশটা স্বাধীন করেছি। আমাদের চিন্তা ছিল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করার। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ও আহ্বানও ছিল তাই। কিন্তু এখনও তা পূরণ হয়নি। দেশটা তো এখনও অনেক পিছিয়ে আছে।’’
এর কারণ কী?
‘‘বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে পুনর্বাসিত করেন। ফলে পরাজিত শক্ররা হতে থাকে শক্তিশালী। ভূতের নাকি পা থাকে পেছন দিকে। তারা সে রকম দেশটাকে পেছনে নিয়ে গিয়েছে।’’
স্বাধীন দেশে ভালো লাগার অনুভূতি জানতে চাই আমরা। মুচকি হেসে তিনি বলেন:
‘‘মুক্তিযুদ্ধে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সময়টা উৎসর্গ করেছিলাম। এখন নতুন প্রজন্মের মাঝে যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেখি তখন খুব ভালো লাগে। কিছুদিন আগেও অনেক বুদ্ধিজীবীকে বলতে শুনেছি যে, এরা নষ্ট প্রজন্ম। কিন্তু তারা যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চ করে প্রমাণ করেছে, দেশের প্রয়োজনে তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের মতো ভূমিকা রাখতে পারে।’’
পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি আশা নিয়ে তাদের উদ্দেশে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন:
‘‘আমরা একটা ভৌগোলিক কাঠামো, পতাকা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশটাকে অর্থনৈতিকভাবে তোমাদেরই সমৃদ্ধ করতে হবে। তোমরা ত্যাগী, সাহসী আর প্রতিবাদি হইও। মেধাবী হয়ে শুধু নিজের স্বার্থ চিন্তা করে দেশ ত্যাগ কর না। ভালোবেসে নিজের দেশের পাশে থেক।’’
সংক্ষিপ্ত তথ্য:
নাম: যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা নৌ কমান্ডো মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।
ট্রেনিং করেন: ৩ মাসের নৌ কমান্ডো ট্রেনিং নেন ভারতের পলাশীতে, ভাগিরথী নদীর তীরে। নৌ কমান্ডো নং ছিল- ০০৬০।
যুদ্ধ করেছেন: ‘অপারেশন জ্যাকপট’এর আওতায় মংলা বন্দরের বেশ কিছু জাহাজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেন। কমান্ডার ছিলেন প্রয়াত আহসান উল্লাহ বীর প্রতীক। পরে ৯ নং সেক্টরের অধীনে স্থলযুদ্ধ করেন ভাতশালা, দেবহাটা থানা যুদ্ধ, কুলিয়া ব্রিজ অপারেশন প্রভৃতিতে অংশ নেন।
যুদ্ধাহত: ১৮ আগস্ট, ১৯৭১। ‘অপারেশন জ্যাকপট’ শেষে ফেরার পথে সাতক্ষীরার বুদহাটাতে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বন্দি হন। তারা তাঁর চোখ বেঁধে, সারা শরীরে রড দিয়ে পেটায়। এক পর্যায়ে তাঁর দু’হাতের ওপর দু’জন দাঁড়িয়ে পড়ে। আরেক জন রড দিয়ে পায়ের তলায় পেটাতে থাকে। মারের আঘাতে তাঁর মুখের সামনের সারির কিছু দাঁত ভেঙে যায়। ইটের খোয়ার রাস্তায় জিপ গাড়ির সঙ্গে তাঁর পা বেঁধে টেনে নিয়ে যায়। ফলে পেটের চামড়া উঠে গিয়ে রক্তাক্ত হয়। পাকিস্তানি সেনাদের বেয়নেটের আঘাত এখনও তাঁর বাঁ হাতের কব্জিতে রয়ে গেছে।
লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪
© 2018, https:.